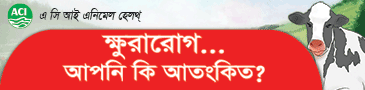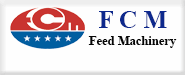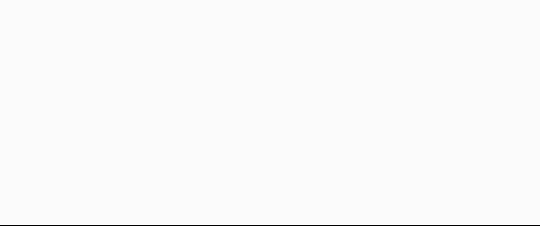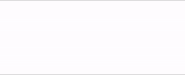а¶Єа¶ЃаІАа¶∞а¶£ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є: а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶Ьගටඌ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ: පа¶ХаІНටග, а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶У а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶∞ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶Ха¶∞аІНටаІНа¶∞аІАа•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞аІЛඕගට а¶Па¶Х а¶ЕථථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Х а¶єа¶≤аІЗථ බаІЗа¶ђаІА බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња•§ ටගථග පаІБа¶ІаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞ ථථ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х පа¶ХаІНටග, а¶Па¶Х а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІА а¶ЪаІЗටථඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඁаІВа¶∞аІНа¶§а¶ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ ථඌඁаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З ථගයගට а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞аІНටඌ, вАШබаІБа¶∞аІНа¶Ча¶ЊвАЩ а¶Еа¶∞аІНඕ вАШඃගථග බаІБа¶∞аІНа¶Чටග ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞аІЗථвАЩа•§ ඙аІМа¶∞а¶Ња¶£а¶ња¶Х а¶ХඌයගථගටаІЗ ටගථග බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ѓ ථඌඁа¶Х а¶Еа¶ЄаІБа¶∞а¶ХаІЗ а¶ђа¶І а¶Ха¶∞аІЗ ඁඌථඐа¶Ьඌටගа¶ХаІЗ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ, а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ටගථග а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶Ьගටඌ, а¶Еа¶ЬаІЗаІЯ, а¶ЕබඁаІНа¶ѓ а¶Па¶Х ථඌа¶∞аІАа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§
බаІЗа¶ђаІА බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶∞ ඙аІМа¶∞а¶Ња¶£а¶ња¶Х ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶У а¶∞аІВ඙ඐаІИа¶ЪගටаІНа¶∞аІНа¶ѓ:
බаІЗа¶ђаІА බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶ђа¶єаІБඁඌටаІНа¶∞а¶ња¶Ха•§ ටගථග а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶ња¶Ха¶Њ, а¶Еа¶ЃаІНа¶ђа¶ња¶Ха¶Њ, а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ѓа¶ЊаІЯа¶Њ, а¶ђаІИа¶ЈаІНа¶£а¶ђаІА, а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ѓа¶ЊаІЯа¶Њ, а¶ХඌටаІНа¶ѓа¶ЊаІЯථаІА, а¶Ѓа¶єа¶ња¶Ја¶Ња¶ЄаІБа¶∞ а¶Єа¶Ва¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶£аІА ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІА а¶ЗටаІНඃඌබග ථඌඁаІЗ ඙аІВа¶Ьගටඌ а¶єа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ බපа¶≠аІБа¶Ьа¶Њ а¶∞аІВ඙а¶Яа¶њ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ, а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ යඌටаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶ХаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶ЄаІНටаІНа¶∞, ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Х පа¶ХаІНටග, а¶Єа¶Ња¶єа¶Є, а¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶У а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඐඌයථ а¶Єа¶ња¶Ва¶є (а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ђа¶Ња¶Ш) а¶Па¶ђа¶В а¶Ѓа¶єа¶ња¶Ја¶Ња¶ЄаІБа¶∞ а¶ђа¶ІаІЗа¶∞ බаІГපаІНа¶ѓ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ѓаІБබаІНа¶Іа¶ЬаІЯаІА а¶∞аІВ඙а¶ХаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶З а¶∞аІВ඙аІЗ ටගථග පаІБа¶ІаІБ а¶Еа¶ЄаІБа¶∞ථඌපගථаІА ථථ, а¶ђа¶∞а¶В ඁඌථඐඪඁඌа¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІВа¶≤ටඌа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§
а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ:
යගථаІНබаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ ඙а¶∞а¶Ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග, а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶Жබග පа¶ХаІНа¶§а¶ња•§ ටගථග පගඐаІЗа¶∞ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА ඙ඌа¶∞аІНඐටаІА, а¶Ха¶Ња¶∞аІНටගа¶Х а¶У а¶Ча¶£аІЗපаІЗа¶∞ а¶ЬථථаІА а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶Ња¶≤аІАа¶∞ а¶Па¶Х а¶∞аІВа¶™а•§ පඌа¶ХаІНට а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗ ටගථග а¶Єа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ЪаІНа¶Ъ а¶Жа¶∞а¶Ња¶ІаІНа¶ѓ බаІЗа¶ђаІА, а¶ђаІИа¶ЈаІНа¶£а¶ђ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБа¶∞ а¶ЕථථаІНට а¶Ѓа¶ЊаІЯа¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯ, а¶Жа¶∞ පаІИа¶ђ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗ ටගථග පගඐаІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶ЩаІНа¶ЧගථаІАа•§ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£аІЗ а¶ѓаІЗඁථ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ха¶£аІНа¶°аІЗаІЯ, බаІЗа¶ђаІА, а¶Ха¶Ња¶≤а¶ња¶Ха¶Њ а¶У а¶ЃаІОа¶ЄаІНඃ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶®а¶Њ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ, ටаІЗඁථග а¶Ѓа¶єа¶Ња¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я ඙а¶∞аІНа¶ђаІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІЗථаІЛ඙ථගඣබаІЗ а¶єаІИඁඌඐටаІАа¶ХаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ЧඐටаІЗ පаІНа¶∞аІАа¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£аІЗа¶∞ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ѓа¶ЊаІЯа¶Ња¶ХаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓаІЗ а¶У а¶Жа¶ЧඁථаІА а¶ЧඌථаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ:
а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටග а¶Па¶Х а¶Жа¶ђаІЗа¶Ча¶Шථ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юа¶§а¶Ња•§ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ а¶У а¶Жа¶ЧඁථаІА а¶ЧඌථаІЗ ටගථග පගඐа¶Ьа¶ЊаІЯа¶Њ ඙ඌа¶∞аІНඐටаІА а¶∞аІВ඙аІЗ ඙ගටаІГа¶ЧаІГа¶єаІЗ а¶Жа¶ЧඁථаІЗа¶∞ а¶ЖථථаІНබඁаІЯ බගථа¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ ඪ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶®а¶ЊаІЯ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗථ а¶Па¶Х а¶Жබа¶∞аІНප ථඌа¶∞аІА, а¶Па¶Х ඁඁටඌඁаІЯаІА а¶Ѓа¶Њ, а¶Па¶Х а¶ХථаІНа¶ѓа¶Њ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Чඁථ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Ша¶∞аІЗ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶єа•§ а¶Па¶З а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ පаІБа¶ІаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В ඙ඌа¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶ња¶Х, а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶У а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Ѓа¶ња¶≤ථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§
බаІБа¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶ЊаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪ а¶У а¶≠аІМа¶ЧаІЛа¶≤а¶ња¶Х а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞:
а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶ЊаІЯ බаІБа¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶ЊаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට බаІНඐඌබප-ටаІНа¶∞аІЯаІЛබප පටඌඐаІНබаІАටаІЗа•§ а¶ЬථපаІНа¶∞аІБටග а¶ЕථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬපඌයаІАа¶∞ ටඌයගа¶∞඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Ха¶Ва¶Є ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ ඙аІНа¶∞ඕඁ පඌа¶∞බаІАаІЯа¶Њ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶єа¶Њ а¶ЖаІЬа¶ЃаІНа¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶Еа¶Єа¶Ѓ, а¶ЙаІЬа¶ња¶ЈаІНа¶ѓа¶Њ, а¶Эа¶ЊаІЬа¶Ца¶£аІНа¶° а¶У а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶Па¶Яа¶њ ථඐа¶∞ඌටаІНа¶∞а¶њ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ЙබаІНඃඌ඙ගට а¶єаІЯа•§ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗ බаІБа¶ђа¶Ња¶∞ බаІБа¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶ЊаІОа¶Єа¶ђ ඙ඌа¶≤ගට а¶єаІЯ, පඌа¶∞බаІАаІЯа¶Њ (а¶ЖපаІНඐගථ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ) а¶У ඐඌඪථаІНටаІА (а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ)а•§ а¶Па¶З а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ පаІБа¶ІаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Ра¶ХаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЙаІОа¶Єа•§
බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ: පа¶ХаІНටගа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Х:
බаІЗа¶ђаІА බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ а¶ЃаІВа¶≤ට පа¶ХаІНටගа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§ ටගථග ථඌа¶∞аІА පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶Єа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ЪаІНа¶Ъ а¶∞аІВ඙, ඃගථග а¶Еа¶ЄаІБа¶∞ පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗ ඁඌථඐа¶Ьඌටගа¶ХаІЗ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ, а¶Єа¶Ња¶єа¶Є, а¶ЖටаІНඁඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶У а¶ЄаІГа¶ЬථපаІАа¶≤а¶§а¶Ња•§ а¶Па¶З පа¶ХаІНටග පаІБа¶ІаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶У а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Ха•§ ථඌа¶∞аІАа¶∞ а¶ХаІНඣඁටඌаІЯථ, ඁඌටаІГටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶∞аІНඃඌබඌ а¶Па¶ђа¶В ථඌа¶∞аІАа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЬථපаІАа¶≤ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Х а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ а¶Жа¶Ьа¶У ඙аІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶Ха•§
а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶У බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х:
а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶ЕටаІНඃථаІНට ථගඐගаІЬа•§ පа¶∞аІОа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ѓа¶Цථ ඲ඌථ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗ පගඣ а¶Іа¶∞аІЗ, ඁඌආаІЗ а¶ЄаІЛථඌа¶≤а¶њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌа¶∞ а¶Жа¶≠а¶Њ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗ, ටа¶Цථа¶З බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආගට а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯа¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶Йа¶∞аІНа¶ђа¶∞ටඌ а¶У а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§ а¶ХаІГа¶Ја¶Х а¶ѓаІЗඁථ а¶Ца¶∞а¶Њ, ඐථаІНа¶ѓа¶Њ, а¶ХаІАа¶Я඙ටа¶ЩаІНа¶Ч а¶У а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х පаІЛа¶Ја¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶≤аІЬа¶Ња¶З а¶Ха¶∞аІЗථ, ටаІЗඁථග බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ а¶≤аІЬа¶Ња¶З а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Еа¶ЄаІБа¶∞ පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Ѓа¶ња¶≤ථ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶ХаІЗ а¶ХаІГа¶Ја¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞аІЗа¶∞а¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§
බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ ඙аІВа¶Ьа¶Њ: а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х පа¶ХаІНටග:
බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ ඙аІВа¶Ьа¶Њ පаІБа¶ІаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х පа¶ХаІНа¶§а¶ња•§ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІАа¶£ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ђаІЗට පаІНа¶∞а¶Ѓ а¶У а¶ЖථථаІНබаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єаІЯ, а¶ѓа¶Њ а¶ХаІГа¶Ја¶ХබаІЗа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х පа¶ХаІНටග а¶ЬаІЛа¶Ча¶ЊаІЯа•§ ථඌа¶∞аІАа¶∞ පа¶ХаІНටග, а¶Ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ХаІНඣඁටඌ а¶У ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЬථපаІАа¶≤ටඌа¶ХаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶∞аІВ඙аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ПටаІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ, а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶Еа¶∞аІНඕථаІИටගа¶Х а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ха¶Ња¶£аІНа¶° ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග, ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶У а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Ра¶ХаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Еа¶Ва¶ґа•§
а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶У බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶ХаІА а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ:
а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ බගථаІЗ а¶Ьа¶≤а¶ђа¶ЊаІЯаІБ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ, а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶У ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞аІЛ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶Па¶ЄаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣඌ඙а¶ЯаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶ХаІА පа¶ХаІНටග а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ බаІЗаІЯ, а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Іа¶Њ а¶ЬаІЯ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Єа¶ЃаІНа¶Ѓа¶ња¶≤ගට а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶ЊаІЯа•§ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗථ а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶Ха¶∞аІНටаІНа¶∞аІА, ඃගථග а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ХаІЗ පаІБа¶ІаІБ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Њ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЙаІОа¶Є а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§
а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶Ьගටඌ බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ පаІБа¶ІаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІМа¶∞а¶Ња¶£а¶ња¶Х а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞ ථථ, ටගථග а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග, а¶ХаІГа¶Ја¶њ, а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶У ථඌа¶∞аІАටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶Ца¶њ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ, а¶ЄаІГа¶Ьථ, පа¶ХаІНටග а¶У а¶Ра¶ХаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶ЪаІНа¶Ыа¶ђа¶ња•§ ටගථග а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ පаІЗа¶Цඌථ, а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ЃаІНа¶Ѓа¶ња¶≤ගටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЬаІЯаІА а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ටඌа¶З බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Њ ඙аІВа¶Ьа¶Њ පаІБа¶ІаІБ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ථаІЯ, а¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ, а¶Па¶Х а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶ња¶Х පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ЙаІОа¶Є, а¶ѓа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ, ඁඌථаІБа¶Ј а¶У ඁථථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ча¶≠аІАа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЬаІЬа¶ња¶§а•§
а¶≤аІЗа¶Ца¶Х: а¶Єа¶ЃаІАа¶∞а¶£ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є, а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶У ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප ඐගපаІЗа¶Ја¶ЬаІНа¶Ю , ඥඌа¶Ха¶Ња•§